বিসর্জন নাটকের প্রশ্ন উত্তর teacj sanjib
বিসর্জন নাটকের প্রশ্ন উত্তর teacj sanjib
রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর। কাহার কি বিসর্জন করিবার উপর ইহার মূল কাহিনীর ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ কর।
‘প্রতিমা বিসর্জনই এই নাটকের শেষ কথা নয়’—এই মন্তব্যটির কথা মনে রেখে
রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’ নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।
রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।
উত্তর। রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’ নাটকটি তাঁর ‘রাজর্ষী’ উপন্যাস অবলম্বন করে রচিত। ‘রাজর্ষি’ নামের এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নাট্যকারের এক বিশেষ ইঙ্গিত ব্যঞ্জিত হয়েছে। সাধারণতঃ কোন সাহিত্য-সৃষ্টির নামকরণের মধ্য দিয়ে লেখক তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্যটিকে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করেন। কোথাও কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র, আবার কোথাও বা কাহিনীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অথবা লেখকের উপলব্ধিগত জীবনসত্য একটা বিশেষ ভাব-ব্যঞ্জনারূপে রচনাটির নামকরণের মধ্য দিয়ে দ্যোতিত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ভাবনার কথা বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে। নামকরণ সম্পর্কে তিনি নিজেই এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন, “রসশাস্ত্রে মূর্তিটি মাটির চেয়ে বেশি, গল্পটিও বিষয়ের চেয়ে বড়। এইজন্য বিষয়টাকে শিরোধার্য করে নিয়ে গল্পের নাম দিতে আমার মন চায় না।” সুতরাং নামকরণের ব্যাপারে তিনি এক ভাবসত্যের উপর জোর দিতে চান একথা সহজেই অনুমেয়।
‘বিসর্জন’ নাটকের নামকরণের তাৎপর্য সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন।’ ‘বিসর্জন—এই নাটকের নামকরণ কোন ভাবকে অবলম্বন করে হয়েছে? আমরা দেখতে পাই যে নাটকের শেষে রঘুপতি প্রতিমা বিসর্জন দিলেন, এই বাইরের ঘটনা ঘটল। কিন্তু এই নাটকে এর চেয়েও মহত্তর এক বিসর্জন হয়েছে। জয়সিংহ তার প্রাণ বিসর্জনে রঘুপতির মনে চেতনার সঞ্চার করে দিয়েছিল।’ সুতরাং নাটকের বিসর্জন নামটি গভীরতার তাৎপর্যের দিকে অঙ্গুলী সংকেত করে।
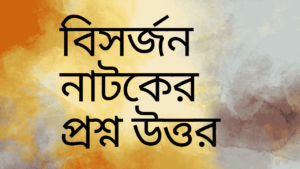
বিসর্জন’ নাটকের নামকরণের সার্থকতা
অধ্যাপক শান্তিকুমার দাশগুপ্ত বলেছেন, ‘উপন্যাসের নাম ‘রাজর্ষি,’ নাটকের নাম ‘বিসর্জন’। উপন্যাসের নামটি স্বতঃই গোবিন্দমাণিক্যের কথা স্মরণ করায়, এখানে তাঁহার ত্যাগ-ধর্মের প্রতিষ্ঠার কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু ‘বিসর্জন’ নামের তাৎপর্য গভীরে নিমজ্জিত না হইয়া বুঝিবার উপায় নাই। অর্থাৎ নামের মধ্যেও বেশ নাটকীয়তা সৃষ্টি করা হইয়াছে।’ তাই নাটকের তাৎপর্য উপলব্ধি করবার জন্য আমাদের নাটকের শেষ পরিণতি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।
‘বিসর্জন’ নাটকে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমধর্মের সঙ্গে রাজপুরোহিত রঘুপতির প্রথাবদ্ধ সংস্কার সর্বস্ব ধর্মের সংঘাত বেঁধেছে। গোবিন্দমাণিক্য তাঁর সমস্ত কিছু ত্যাগ করেও প্রেমধর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। এবং তাঁর সেই আদর্শ রক্ষার জন্য তিনি ঘরের ও বাইরের সমস্ত সুখ-আনন্দ বিসর্জন দিয়েছিলেন। এমন কি বিসর্জনের অর্থ যদি পরিত্যাগ হয় তাহলে শেষপর্যন্ত তিনি রাজ্য-রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করার সংকল্পও গ্রহণ করেন। আর সেই প্রেমধর্মের আদর্শকে জয়যুক্ত করার জন্য রঘুপতির অনুচর ও সেবক জয়সিংহেরও প্রাণ বিসর্জনের আবশ্যক হয়। এবং জয়সিংহের আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়েই রাজপুরোহিত রঘুপতি এবং মহারাণী গুণবতীর অন্তরে প্রেমধর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
গোবিন্দমাণিক্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন এবং জীবনের আদর্শ আত্মবিসর্জনের প্রেরণা দিচ্ছে জয়সিংহকে আর জয়সিংহের আত্মবিসর্জন সমস্ত নাটকের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। রঘুপতির এতদিনের সংস্কারাচ্ছন্ন মনে জাগে সংশয় ও তাঁর জীবনের উপলব্ধ সত্য পরিণামমুখী হয়ে ওঠে।
জয়সিংহের আত্মবিসর্জনই এই নাটকের প্রধানতম ঘটনা, কিন্তু সেই ঘটনায়ই নাটকের সমাপ্তি নয়, একটি মানবজীবনের বিসর্জনে আর একটি মানবহৃদয়ে সত্যের উপলব্ধি জেগে ওটাই এই নাটকের মুখ্য প্রতিপাদ্য। এই জয়সিংহের আত্মত্যাগের উপরই রবীন্দ্রনাথ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ জয়সিংহের আত্মত্যাগের ফলেই রঘুপতি সুস্পষ্টভাবে এই সত্যকে অনুভব করতে পারলেন যে, প্রেম হিংসার পথে চলে না, বিশ্বমাতার পূজা জীববলির মধ্য দিয়ে সার্থক হয় না, সার্থক হয় প্রেমের আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে। ফলে বহুদিনের অর্জিত সংস্কার-বোধ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। দেবীর প্রতিমা বিসর্জিত হলো গোমতী নদীর জলে। তাই রঘুপতি মহারাণী গুণবতীর দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা-অর্ঘ্যকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, ‘কোথাও সে/নাই। ঊর্ধ্বে নাই, নিম্নে নাই, কোথাও সে/নাই, কোথাও সে ছিল না কখনো’। কিন্তু দেবীর বিসর্জনই শেষ কথা নয়, রঘুপতির কথায় রাণী গুণবতী সচকিত হয়ে ওঠেন, নিজের অহংকারকে বিসর্জন দিয়ে ফিরে আসেন মহাদেব তুল্য স্বামীর কাছে। রাজ্য বিসর্জন দিয়েও রাণীকে ফিরে পেয়ে পরম আনন্দে গোবিন্দমাণিক্য বলে ওঠেন,
বিসর্জন নাটকের প্রশ্ন উত্তর teacj sanjib
‘গেছে পাপ। দেবী আজ এসেছে ফিরিয়া
আমার দেবীর মাঝে।’
অপরদিকে জয়সিংহকে রাজরক্ত এনে দিতে হবে। তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সে তার জীবনের আদর্শ রাজা গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা না করে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। তাই রঘুপতি যখন জিজ্ঞাসা করেন, ‘জয়সিংহ, রাজরক্ত কই?’ জয়সিংহ তার উত্তরে জানায়,— ‘আছে আছে। ছাড়ো মোরে।
নিজে আমি করি নিবেদন।’
জয়সিংহের প্রতি রঘুপতির স্নেহ-প্রেমের সীমা ছিল না। জয়সিংহের মৃত্যুতে রঘুপতি জেগে উঠলেন, তাঁর দীর্ণ কণ্ঠে শোনা গেল—
‘জয়সিংহ, বৎস মোর, হে গুরু বৎসল
ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছু নাহি চাহি!’
যে অপর্ণাকে তিনি এতদিন দূর দূর করে তাড়িয়েছেন, সেই অপর্ণাকেই কাছে টেনে নেন, তাঁর মর্মস্পর্শী রুণ্ঠে ধ্বনিত হয়,—‘আয় মা অমৃতময়ী।’ অপর্ণার মধ্য দিয়ে তিনি প্রেমের বাণীটির উপলব্ধি করতে চাইলেন।
তাই স্বচ্ছন্দে বলা যায় জয়সিংহের আত্মাহুতিই নাটকের ভাবসত্যটিকে ফুটিয়ে তুলেছে। জয়সিংহ যেমন প্রেমকে যথার্থভাবে অনুভব করতে পেরেছিল বলেই আত্মদান করেছে, রঘুপতিও সেইরূপ জয়সিংহের আত্মদানের মাধ্যমে প্রেমের মর্মকথাটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই দেবী প্রতিমার বিসর্জন ঘটিয়েছেন আর তাঁর হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সত্যের জ্যোতি।
বিসর্জন নামটির মধ্য দিয়ে নাট্যকার এই ভাবসত্যকেই তুলে ধরেছেন। তাই নাটকটির নামকরণ যথার্থ ও সার্থক হয়ে উঠেছে।
‘বিসর্জন’ নাটকের নায়ক কে? নাট্যকাহিনী বিশ্লেষণ করে যুক্তিসহ আলোচনা কর।
অথবা,
গোবিন্দমাণিক্য, জয়সিংহ অথবা রঘুপতি—এদের মধ্যে কাকে তুমি বিসর্জন নাটকের
নায়ক বলে মনে কর, যুক্তিসহ আলোচনা করে দেখাও।
উত্তর : নাট্যকার যে চরিত্রটি অবলম্বন করে তাঁর মূল বক্তব্যকে রূপায়িত করেন তিনিই নাটকে নায়কের মর্যাদা লাভ করে থাকেন। অর্থাৎ নাটকের মূল অভিপ্রায় ও প্রতিপাদ্য বিষয় যে চরিত্রকে অবলম্বন করে উপস্থাপিত হয়, তিনিই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে বিবেচিত হন।
‘বিসর্জন’ নাটকে তিন প্রধান চরিত্র রঘুপতি, গোবিন্দমাণিক্য ও জয়সিংহ—এরা প্রত্যেকেই নাটকের নায়ক হবার দাবি রাখে। এখন কার দারী যুক্তিসঙ্গত সে বিষয়ে বিচার বিবেচনার প্রয়োজন আছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আলংকারিকের মতে নাটকের নায়ক হবেন
বিসর্জন নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র
কেন্দ্রীয় চরিত্র, ধীরোদাও গুণবিশিষ্ট এবং সর্বগুণান্বিত। তবে ট্র্যাজেডি বা করুণ রসাত্মক নাটকে এই সর্বগুণান্বিত চরিত্রটির বেদনাবিদ্ধ পরিণতি দর্শক ও পাঠকদের মনে যুগপৎ করুণা ও ভীতি সঞ্চার করে। এবং সেই কারুণ্যের মধ্যে একটা বিস্ময়বোধ জাগ্রত হয়।
‘বিসর্জন’ নাটকটি শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিতে নায়কের জীবন যন্ত্রণা এক মর্মান্তিক পরিণতির পথে অগ্রসর হয়। সেক্ষেত্রে কোন চারিত্রিক দুর্বলতার পথ ধরেই হোক বা অনিবার্য পরিণতির অসহায় বোধের মধ্যেই হোক মহিমান্বিত ব্যক্তি-চরিত্রটির পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ‘বিসর্জন’ নাটকের নায়ক বিচারের প্রসঙ্গে উপরোক্ত রীতি পদ্ধতির কথা মনে রাখতে হবে।
‘বিসর্জন’ নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে যে, প্রেম হিংসার পথে চলে না, বিশ্বমাতার পূজা প্রেমের দ্বারাই সাধিত হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে এই প্রেমের প্রতিষ্ঠাই নাট্যকারের লক্ষ্য। সুতরাং যে চরিত্রের মাধ্যমে নাটকের এই
বিসর্জন নাটকের প্রশ্ন উত্তর
মূল ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকেই আমরা কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে স্বীকার করে নিতে পারি। এই মানদণ্ডে বিচার করলে আমরা তিন প্রধান চরিত্র, রঘুপতি, গোবিন্দমাণিক্য ও জয়সিংহের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সবার আগে আলোচনা করা দরকার। প্রথমে রঘুপতির কথা ধরা যাক । প্রাচীন প্রথাবদ্ধ ধর্মীয় সংস্কারের প্রতিভূ হিসাবে রঘুপতি রাজশক্তির বিরুদ্ধে সম্মুখ • সমরে লিপ্ত হয়েছেন। এবং এই সমরে জয়লাভের লক্ষ্যেই তিনি তাঁর যাবতীয় সমর উপকরণ সজ্জিত করেছেন। তাঁর কূটনৈতিক কৌশল, নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র সংঘটিত করার চেষ্টা করেছেন। ফলে তাঁর চারিত্রিক মহিমা অপেক্ষা দম্ভের প্রকাশই প্রাধান্য লাভ করেছে। তাঁর মধ্যে যদিও আমরা আত্মশক্তির প্রাবল্য ও সংকল্পের দৃঢ়তা প্রকাশ লক্ষ্য করি তা কিন্তু তাঁর অন্ধ বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই।) সেজন্য তা নীতিহীন অন্ধ আক্রোশের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মহৎ আদর্শের পরিপন্থী হয়ে উঠেছে। এখানে না আছে নৈতিকতার মহিমা, না আছে মহানুভবতা। শেষপর্যন্ত তাই তিনি অশুভ শক্তির প্রতীক হয়ে পর্যুদস্ত হয়েছেন। এই সমস্ত কারণে নায়ক চরিত্রের মর্যাদা ও গৌরব অর্জনে ব্যর্থ হন। এছাড়া জয়সিংহের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক স্নেহ থাকলেও নীতিজ্ঞান বর্জিতা অন্ধ ক্ষমতালোলুপতা সেই স্নেহকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সেজন্য রাজা গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করার কাজে জয়সিংহকে নিযুক্ত করেও তাঁর মধ্যে কোনরূপ অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় নি। এবং তার মধ্যে কোন স্বাভাবিক ট্রাজিক পরিণতিও লক্ষ্য করা যায় নি। সুতরাং নায়ক চরিত্রের মর্যাদা রঘুপতির প্রাপ্য নয়।
নায়ক চরিত্রের বিচারে দ্বিতীয় প্রধান চরিত্র গোবিন্দমাণিক্যের ভূমিকা আলোচনা করা যেতে পারে। ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসে রাজা গোবিন্দমাণিক্যকেই কেন্দ্র করে নায়কের ভূমিকায় রাখা হয়েছে। ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসের কাহিনী ‘বিসর্জন’ নাটকের কাহিনীকে অনেক দূরে ফেলে প্রসারিত হয়েছে। তিনি সেখানে তাঁর অভীষ্ট প্রেমধর্মকে চরিতার্থ করতে পেরেছেন। কিন্তু বিসর্জন নাটকের কাহিনীতে গোবিন্দমাণিক্যের সেই ভূমিকা নেই। অবশ্য তাঁর মধ্যে নায়কোচিত অনেক গুণ আছে। তাঁর উদার স্বভাব-মহিমা এবং আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা তাঁর চরিত্রকে একটি বিশেষ গৌরব দান করেছে। কিন্তু নায়ক চরিত্রের মধ্যে যে সংগ্রামশীলতা থাকা দরকার তা তাঁর চরিত্রে অনুপস্থিত। তিনি রাজপুরোহিত রঘুপতির সঙ্গে সংঘর্ষে, রাণী গুণবতীর বিরোধিতায় বা ভ্রাতা নক্ষত্র রায়ের বিশ্বাসঘাতকতায় মর্মাহত হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু ক্ষেত্রসুলভ বীরত্বে তিনি এই সমস্ত আঘাতের বিরুদ্ধে ঝলসে উঠতে পারেন নি। আরও একটা দিক ভেবে দেখার মত। ডঃ সুবোধ সেনগুপ্তের ভাষায় বলা যায়, “শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডিতে
শুধু যে বাইরের উত্থান পতনের কথা সূচীত হয় তাহা নহে, নায়কের মনের নানা ভাবের ঘাত প্রতিঘাতের চিত্রও দেওয়া হইয়া থাকে এবং শেষোক্ত দ্বন্দ্বই শেক্সপীয়র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের নাটকের প্রধান উপজীব্য। কিন্তু ‘বিসর্জন’ নাটকে পরস্পর বিরোধী দুইটি নায়কের মনে দ্বন্দ্ব নাই। ফলে গোবিন্দমাণিক্য এক দ্বন্দ্বহীন, বিকাশহীন ও সংশয়হীন প্রতীক চরিত্র হয়ে পড়ায় এই নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও নায়কের মর্যাদায় ভূষিত হতে পারেন নি।
এবার ‘বিসর্জন’ নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র জয়সিংহের ভূমিকা আলোচিত হতে পারে। জয়সিংহ রাজপুরোহিত রঘুপতির পালিত পুত্র ও দেবীর মন্দিরের সেবক। কাজেই রঘুপতির প্রতি তার আনুগত্য থাকা স্বাভাবিক আবার অন্যদিকে মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যকেও সে কম শ্রদ্ধার চোখে দেখে নি। ফলে দুই মতাদর্শের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে আন্দোলিত হয়েছে, অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। নাটকে বিরোধের অবসান হয়েছে জয়সিংহের মৃত্যুতে। জয়সিংহের আত্মদানেই রঘুপতির চেতনালোকে অরুণোদয় হয়েছে। এজন্য অনেকে জয়সিংহের ভূমিকাকে গুরুত্ব আরোপ করে তাকেই নায়ক চরিত্রের মর্যাদা দিতে চান। কিন্তু এখানে জয়সিংহের আত্মবিসর্জনের পরই নাটকের যবনিকাপাতের ঘটনাকে তাঁরা নাট্যদ্বন্দ্বের কেন্দ্রে স্থাপন করতে ইচ্ছুক নন। তাঁদের মতে নাটকে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল অন্য কারণে এবং তার অবসানের জন্য জয়সিংহের আত্মবলিদানের প্রয়োজন ছিল।
এক্ষেত্রে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে নাটকীয় সংঘাতের প্রাণকেন্দ্রে জয়সিংহের ভূমিকা কতটা অপরিহার্য ছিল। যেহেতু নাটকে দুই বিরোধী ভাবাদর্শের দ্বন্দ্ব সংঘাত দেখানো নাট্যকারের মূল লক্ষ্য সেখানে রঘুপতির প্রতি কর্তব্যবোধে ও গোবিন্দমাণিক্যের সত্যাদর্শে জয়সিংহের ব্যক্তিসত্তা দ্বিধাবিভক্ত। তার চিত্তে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচল মনোবৃত্তি হৃদয়ের তন্ত্রিতে তন্ত্রিতে ঢেউ তুলেছে। তার মনে রঘুপতির প্রথাগত সংস্কারের সঙ্গে রাজার উদার ভাবাদর্শের বিরোধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। আবার অপর্ণার প্রেম।দর্শও তাকে কম বিচলিত করে নি। ফলে শেষপর্যন্ত এ দ্বন্দ্বের সমাধান করতে না পেরে তাকে আত্মহননের পথকে বেছে নিতে হয়েছে। এভাবে নাটকের মূলভাবটির স্পন্দন সর্বাপেক্ষা স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে জয়সিংহের দ্বিধাদীর্ণ চরিত্রে। কাজেই নাটকের ট্রাজিক পরিণতি জয়সিংহকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। আর তার মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করেই রঘুপতি চরিত্রের বিবর্তন সম্ভব হয়েছে।
সুতরাং দ্বন্দ্বের অবসান ও অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়া যদি নাটকের ট্রাজিক রস উৎপাদনে সহায়তা করে তাহলে বলতেই হবে জয়সিংহ চরিত্রই সেখানে সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

খুব সুন্দর এবং সহজ সরল ভাষায় নোটগুলো লেখা হয়েছে। আমি অনেক উপকৃতি হলাম এবং যারা পড়বে তারাও অনেক উপকৃত হবে। ধন্যবাদ এত সুন্দর করে উপস্থাপনের জন্য।