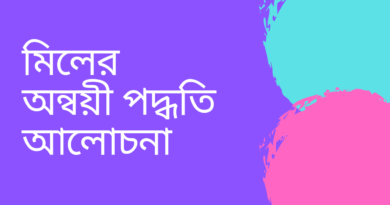কার্যকারণ সম্পর্কে প্রসক্তি সম্বন্ধ বা অনিবার্য সম্বন্ধ মতবাদ আলোচনা
কার্যকারণ সম্পর্কে প্রসক্তি সম্বন্ধ বা অনিবার্য সম্বন্ধ মতবাদ আলোচনা
কার্যকারণ সম্পর্কে প্রসক্তি সম্বন্ধ বা অনিবার্য সম্বন্ধ মতবাদ
কার্যকারণ সম্পর্ক
কার্যকারণ সম্পর্কে প্রসক্তি সম্বন্ধ অনিবার্য সম্পৰ্ক:
বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ কার্যকারণের মধ্যে এক অনিবার্য সম্পর্ক স্বীকার করেন এবং তাঁরা বলেন যে, এ ধরনের সম্পর্ক হল ব্যতিক্রমহীন। কার্য ও কারণের এই সার্বিক সম্বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দাবি করা হয় যে, প্রত্যেকটি কার্যেরই একটি কারণ আছে। একই রূপ কারণ থেকে একই রূপ কার্য সংঘটিত হয়। কোথাও তার কোনো ব্যতিক্রম হয় না। সবসময়েই একই কারণ থেকে একই কাজ হয়ে থাকে।
প্রসক্তি সম্বন্ধ:
বুদ্ধিবাদীদের মতে, কারণ হল কার্যের উৎপাদক বা সৃষ্টিকারক এবং সেইজন্য কারণের প্রকৃতি বা প্রকারের অনুরূপভাবে কার্যটিও ঘটে। সুতরাং কার্য ও কারণের মধ্যে একপ্রকারের অনিবার্যতা বা অবশ্যম্ভাবিতার সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ যৌক্তিক বা তার্কিক অনিবার্যতারূপেই স্বীকৃত। এই যৌক্তিক বা তার্কিক অনিবার্যতাকেই বলা হয় প্রসক্তি সম্বন্ধ (entailment relation)। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ এই প্রসক্তি সম্বন্ধ বা অনিবার্য সম্বন্ধের ওপর ভিত্তি করে কার্যকারণ সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করেছেন। কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ প্রসঙ্গে বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের এরূপ মতবাদকে বলা হয় প্রসক্তি তত্ত্ব (entailment theory)।
কার্যকারণ সম্পর্কে প্রসক্তি সম্বন্ধ বা অনিবার্য সম্বন্ধ মতবাদ
কারণের মধ্যেই কার্য নিহিত:
এই মতবাদ অনুযায়ী দাবি করা হয় যে, কার্য ও কারণের মধ্যে একপ্রকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ, কার্যের সংঘটন একটি নতুন ঘটনারূপে স্বীকৃত হলেও, তা আগে থেকেই কারণের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় নিহিত। কার্য তাই কারণকে শুধুমাত্র অনুগমনই করে না, কারণ উপস্থিত হলে কার্যটিও অবশ্যই উপস্থিত হয়। এর কোনো রকমের হেরফের কোথাও হয় না।
প্রসক্তি তত্ত্বের মূল বক্তব্যসমূহ (Main Tenets of Entailment Theory)
কার্যকারণ সম্বন্ধ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রসক্তি তত্ত্বে মূলত যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, নীচে সেগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।
হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের সম্পর্কের অনুরূপ হিসেবে কার্যকারণ সম্পর্ক
আমরা বলতে পারি,
সকল লেখক হন শিক্ষিত। মৃণালবাবু হন লেখক। [হেতুবাক্য]
[সিদ্ধান্ত] :: মৃণালবাবু হন শিক্ষিত।
ওপরের এই যুক্তিটি হল একটি অবরোহাত্মক যুক্তি। এখানে প্রথম দুটি বাক্যকে বলা হয় যুক্তিবাক্য। যুক্তিবাক্য দুটির ভিত্তিতে যে তৃতীয় বাক্যটি পাওয়া যায়, সেটিকে বলে সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে যুক্তিটি একটি বৈধ যুক্তিরূপে পরিগণিত হয়। একটি বৈধ অবরোহমূলক যুক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সিদ্ধান্তটি অনিবার্যভাবে যুক্তিবাক্য (premises) থেকে নিঃসৃত। যুক্তিবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যেকার এরূপ সম্পর্কটি একপ্রকার প্রসক্তি সম্বন্ধ। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আমরা সিদ্ধান্তে (conclusion) যুক্তিবাক্যের বিষয়কেই স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করি।
সিদ্ধান্তের বক্তব্যটি যুক্তিবাক্যে প্রচ্ছন্ন:
এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই যুক্তিবাক্যের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে থেকেই যায়। অর্থাৎ, সিদ্ধান্তে আমরা এমন কিছুই উল্লেখ করতে পারি না, যা যুক্তিবাক্যের মধ্যে নেই। এখানে সিদ্ধান্ত তথা “মৃণালবাবু হন শিক্ষিত” যুক্তিবাক্য থেকেই নিঃসৃত। এমন কিছুই সিদ্ধান্তটিতে বলা হয়নি, যা যুক্তিবাক্য দুটির মধ্যে পরোক্ষভাবে নেই।
সিদ্ধান্তের সত্যতা যুক্তিবাক্যের সত্যতা থেকে নিঃসৃত: সিদ্ধান্তটির সত্যতা যুক্তিবাক্য দুটির সত্যত। ওপরই নির্ভরশীল। যুক্তিবাক্য যদি সত্য হয়, তাহলে সিদ্ধান্তটিও সত্য হতে বাধ্য। আবার যুক্তিবাক্য যদি মিথ) হয়, তাহলে সিদ্ধান্তটিও মিথ্যা হয়। অর্থাৎ, যুক্তির ক্ষেত্রে আমরা এমন কোনো দাবি করতে পারি না, যেখানে) যুক্তিবাক্য সত্য অথচ সিদ্ধান্তটি মিথ্যা।
প্রসক্তি সম্বন্ধ হল অনিবার্য সম্বন্ধ:
এরই পরিপ্রেক্ষিতে দাবি করা সংগত যে, এক্ষেত্রে যুক্তিবাক্য ) হেতুবাক্য এবং সিদ্ধান্তের মধ্যকার সম্পর্কটি হল অনিবার্যতার সম্পর্ক। সিদ্ধান্তটির সত্যতা তাই অবশ্য। যুক্তিবাক্যের সত্যতা থেকে প্রসক্ত বা নিঃসৃত (entailed)। সেকারণেই এরূপ সম্পর্ককে বলা হয় প্রসক্তি সম্বন্ধ
কারণের সত্যতার ওপর কার্যের সত্যতা নির্ভরশীল
বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা বলেন যে, দুটি ঘটনা যদি প্রকৃতপক্ষে কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, তাহলে একটি ঘটনা। আর একটি ঘটনাকে অবশ্যই ইঙ্গিত করবে।
উদাহরণ: : ‘p’ এবং ‘q’ নামক দুটি ঘটনা যদি কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, তাহলে তাদের মধ্যে সম্পর্ক। অবশ্যই অনিবার্যতার সম্পর্করূপে স্বীকৃত হবে। সেক্ষেত্রে ‘p’ নামক ঘটনা যদি ঘটে, তবে ‘q’ নামক ঘটনাটিও ঘটবে। এক্ষেত্রে ‘p’ হল কারণ এবং ‘q’ হল কার্য। অথবা বলা যায় যে ‘q’ নামক কার্যটি অকারণে ঘটতে পারে না, তা ‘p’ নামক কারণ থেকেই নিঃসৃত। এই সাংকেতিক উদাহরণ ছাড়াও একটি মূর্ত উদাহরণের মাধ্যমেও বিষয়টিকে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা যেতে পারে। ধরা যাক ‘অগ্নি’ হল কারণ এবং ‘দহন’ হল কার্য। এই দুটি ঘটনার মধ্যে যদি অনিবার্যতার সম্বন্ধ থাকে, তাহলে আমাদের পক্ষে দাবি করা সংগত যে, যেখানেই ‘অগ্নি’ আছে, সেখানেই দহন ক্রিয়া থাকবে। অর্থাৎ, অগ্নির উপস্থিতি দহন ক্রিয়াকে প্রসক্ত করবেই। কোনোক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম ঘটবে না।
↑ ব্যাখ্যা:
আজ পর্যন্ত আমরা যেখানে অগ্নিকে দেখেছি, সেখানেই তার ক্রিয়া হিসেবে ‘দহন’কে উপস্থিত হতে । দেখেছি। অথবা বলা যায়, দহন যেখানেই হয়েছে, তার পিছনে অগ্নির উপস্থিতি অবশ্যই আছে। আমরা এমন কোনো ক্ষেত্র বা উদাহরণ আজ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করিনি, যেখানে অগ্নির উপস্থিতি আছে অথচ দহন ক্রিয়া অনুপস্থিত। এরকম একটিও উদাহরণের উল্লেখ যদি আমরা করতে পারতাম, তাহলে আমাদের পক্ষে কখনোই বলা সংগত হত না যে, অগ্নি এবং দহনের মধ্যে অনিবার্যতার সম্বন্ধ বা প্রসক্তি সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষিত হয়নি বলেই দাবি করা সংগত যে, অগ্নি এবং দহনের মধ্যে প্রসক্তি সম্বন্ধ আছে।
কার্য ও কারণের সম্বন্ধটি তর্কবিজ্ঞানসম্মত
কার্য ও কারণ সম্পর্কে প্রসক্তিবাদীরা বলেন, কার্য ও কারণের মধ্যে যে পূর্বাপর (অর্থাৎ একটি আগে এবং অন্যটি পরে ঘটে) সম্পর্ক দেখা যায়, তা প্রকৃতপক্ষে কালিক (temporal) নয়, তা হল তর্কবিজ্ঞানসম্মত বা ন্যায়গত (logical)। তর্কবিজ্ঞানের মূল যে কাঠামো, তার ওপরে ভিত্তি করেই কার্যকারণের সম্পর্কটি দাঁড়িয়ে আছে। বিশুদ্ধ অবরোহাত্মক অনুমানে যুক্তিবাক্য (premises) এবং সিদ্ধান্তের (conclusion) মধ্যে কোনো কালিক (কালগত) পূর্বাপর সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয় না। কারণ, আমরা জানি যে, এক্ষেত্রে যুক্তিবাক্যসমূহের মধ্যেই সিদ্ধান্তটি নিহিত থাকে। সে কারণে তাদের পূর্বাপর সম্পর্ক শুধুমাত্র চিন্তার ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায়। কারণ, আমরা আগে যুক্তিবাক্যের চিন্তা করি এবং তারপর চিন্তা করি সিদ্ধান্তের। একারণেই আমরা আগে কারণের চিন্তা করি এবং তারপর চিন্তা করি কার্যের। কারণ হল কার্যের হেতু। স্বাভাবিকভাবেই প্রসক্তি মতবাদ অনুযায়ী দাবি করা হয় যে, কারণ এবং কার্যের মধ্যে সম্বন্ধটি হল যৌক্তিক অনিবার্যতার সমৃদ্ধ (relation of logical necessity)।
প্রসক্তি তত্ত্বের সপক্ষে যুক্তি (Arguments for Entailment Theory)
আধুনিক বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ, সাধারণ মানুষ এবং বিজ্ঞানী সম্প্রদায়—সকলেই কার্যকারণ সম্পর্কিত এই অনিবার্যতার সম্বন্ধকে স্বীকার করেছেন। দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজ প্রমুখ বুদ্ধিবাদী দার্শনিক কার্যকারণের এই অনিবার্যতার সম্বন্ধকে স্বীকার করেছেন। এঁরা ছাড়া আরও যেসব আধুনিক দার্শনিক কার্যকারণের এরূপ অনিবার্যতা বা
প্রসক্তি সম্বন্ধকে স্বীকার করেন, তাঁরা হলেন—ইউয়িং (Ewing), ব্ল্যানশাৰ্ড (Blanshard) এবং ব্রড (Broad) প্রমুখ। আধুনিক কালের প্রসক্তিবাদীদের অন্যতম অধ্যাপক ইউয়িং (Ewing) প্রসক্তিবাদের সমর্থনে জোরালো যুক্তির অবতারণা করেছেন। এই যুক্তিগুলি হল—
কারণ থেকে কার্যের অনিবার্যতা অনুমান:
আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে আমরা অনেকক্ষেত্রেই একটি কারণ থেকে তার কার্যটিকে অনুমান করতে পারি। এখন প্রশ্ন হল—কীভাবে আমরা কারণ থেকে একটি কার্যকে অনুমান করতে সক্ষম হই? এর উত্তরে বলা যায় অনিবার্যতার ধারণা থেকেই এরূপ অনুমান সম্ভব। কারণ এবং কার্যের মধ্যে একটা অনিবার্য সম্পর্ক আছে বলেই আমরা কারণ থেকে কার্যে অনুমান করতে সক্ষম হই। কারণ ও কার্যের মধ্যে যদি কোনো প্রকারের অনিবার্যতার সম্বন্ধ না থাকত, তাহলে একটি কারণ থেকে তার কার্যকে যথাযথভাবে অনুমান করা সম্ভব হত না।
উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, “জলপান তৃয়া নিবারণ করে”এক্ষেত্রে ‘জলপান’ হল কারণ এবং ‘তৃষ্ণা নিবারণ’ হল কার্য এবং তাদের মধ্যে সম্পর্কটিও অনিবার্য। কারণ ‘জলপান’ নামক ঘটনাটিকে বিশ্লেষণ করলেই আমরা ‘তৃয়া নিবারণের’ বিষয়টি পেয়ে থাকি। এই দুটি ঘটনার মধ্যে সম্পর্কটি যদি আবশ্যিক না হয়ে আকস্মিক (accidental) হত, তাহলে ‘জলপান’ নামক পূর্ববর্তী ধারণাটিকে বিশ্লেষণ করলে কার্যরূপী অনুবর্তী ধারণা তথা ‘তৃয়া নিবৃত্তি’কে আমরা পাবই—এমন কথা আমরা অনুমান করতে পারতাম না।
কারণ দ্বারা কার্যের যথাযথ ব্যাখ্যা:
কার্যকারণ সম্পর্কে প্রসক্তি সম্বন্ধ বা অনিবার্য সম্বন্ধ মতবাদ
কার্যকারণকে যদি দুটি ঘটনার মধ্যে শুধুমাত্র অগ্রবর্তী (কারণ) এবং অনুবর্তী (কার্য) হিসেবে অভিহিত করা হয়, তাহলে কারণ থেকে কার্যটি ঘটার কোনো ব্যাখ্যা মেলে না। আবার কার্যকারণ সম্বন্ধ যদি দুটি ঘটনার মধ্যে শুধুমাত্র সততসংযোগ (হিউমের মতানুযায়ী) হয় তাহলেও কারণ থেকে কার্যের কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়। এই ধরনের ব্যাখ্যা একমাত্র তখনই সম্ভব, যদি কোনো কারণের মধ্যে কার্য ঘটার হেতুটি (Reason) নিহিত থাকে। সাধারণভাবে হেতুবাক্য থেকে যেমন সিদ্ধান্তের একটা ব্যাখ্যা মেলে, তেমনি কারণ থেকেও কার্যের একটা ব্যাখ্যা মেলে। প্রসক্তি মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে কারণকে কার্যের হেতু হিসেবে অভিহিত করার ফলে, কোনো একটি বিশেষ কারণ থেকে কোনো একটি বিশেষ কার্য ঘটে—তার ব্যাখ্যা মেলে। যেমন, “আগুন দহনক্রিয়া সম্পন্ন করে”—এ ক্ষেত্রে ‘দহনক্রিয়ার’ হেতু হল ‘আগুন’ এবং এই আগুনের উপস্থিতির জন্য আমরা দহনক্রিয়াটিকে যৌক্তিকভাবে অনুমান করতে পারি। সুতরাং দাবি করা যায় যে, হেতু হিসেবে কারণ উপস্থিত থাকার ফলে, তার কার্যের ধারনাটিকে অনুমান করা যায়।
প্রসক্তি তত্ত্বের সমালোচনা (Criticism of Entailment Theory)
বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ কার্যকারণের সম্বন্ধকে প্রসক্তি সম্বন্দ্বরূপে অভিহিত করেছেন। এই প্রসক্তি সম্বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা দাবি করেন যে, কার্য ও কারণের মধ্যে এক প্রকারের অনিবার্য সম্বন্ধ আছে। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ বুদ্ধিবাদীদের এই অনিবার্য সম্বন্ধ তথা প্রসক্তি সম্বন্ধকে স্বীকার করেন না। তাঁরা বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে কার্যকারণের মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধকে নস্যাৎ করেছেন। তাঁদের মধ্যে এই সম্পর্ক আকস্মিক বা তাৎক্ষণিক। এদের মধ্যে কোনো অনিবার্য সম্পর্ক নেই।
অভিজ্ঞতালব্ধ নয়:
অভিজ্ঞতাবাদীরা প্রসক্তিতত্ত্বের সমালোচনা করে বলেন যে, প্রসক্তি সম্বন্ধের বিষয়টিকে কখনোই আমাদের ইন্দ্রিয় সংবেদনের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। তাঁরা বলেন—আমাদের অভিজ্ঞতা আসে ইন্দ্রিয় সংবেদন অথবা ধারণার মাধ্যমে। ইন্দ্রিয় সংবেদনকে বলা ইন্দ্রিয়জ, আর ইন্দ্রিয়জের মাধ্যমে যা পাওয়া যায় তাকেই বলা হয় ধারণা। সুতরাং বলা যায় যে, অভিজ্ঞতার সাহায্যে পাওয়া বিষয় ইন্দ্রিয়জ অথবা ধারণা থেকেই নিঃসৃত হয়। কিন্তু প্রসক্তি সম্বন্ধের বিষয়টি এই দুটি উৎসের কোনোটিই থেকেই পাওয়া যায় না বলে, এরূপ সম্বন্ধটিকে স্বীকার করার কোনো যুক্তিই নেই।
কারণ ও হেতুর তুলনা অযথার্থ:
প্রসক্তিবাদীরা দাবি করেন যে, কার্য ও কারণের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে, তা হল যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত অনিবার্যতার সম্বন্ধ। এই সম্পর্ক হল বৈধ যুক্তির ক্ষেত্রে হেতুবাক্য এবং সিদ্ধান্তের মধ্যে যে সম্পর্ক লক্ষ করা যায়, ঠিক তার অনুরূপ। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদীরা কার্যকারণের মধ্যে হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের সম্পর্ককে আদৌ স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, কার্য ও কারণের মধ্যে এক ধরনের পূর্বাপর সম্বন্ধ লক্ষ করা যায়।
সুতরাং এই সম্পর্ক একপ্রকার কালিক (temporal) সম্পর্ক। কিন্তু হেতুবাক্য এবং সিদ্ধান্তের মধ্যেকার সম্পর্কটি কখনোই কালিক নয় (non-temporal)। সুতরাং, কারণ এবং হেতুর তুলনাটি এখানে যথাযথ নয়। কারণ ও হেতু তাই ভিন্ন ধারণা, তারা অভিন্ন কিছু নয়। বৈধ যুক্তির ক্ষেত্রে আমরা তাই কোনো সিদ্ধান্তের কারণরে নির্ণয় করি না। আমরা শুধুমাত্র তার হেতুকে উল্লেখ করি। কিন্তু কার্যকারণের ক্ষেত্রে আমরা কোনো কার্যের কারণকে নির্ণয় করার চেষ্টা করি। যেমন—ক্ষুধা নিবৃত্তির ক্ষেত্রে তার কারণ হিসেবে খাদ্যকে চিহ্নিত করি।
● কার্যকারণ সম্বন্ধ সম্ভাব্য, অনিবার্য নয়:
অবরোহমূলক বৈধ যুক্তির ক্ষেত্রে হেতুবাক্য বা যুক্তিবাক্য থেকে সিদ্ধান্তটি অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হওয়ার বিষয়টিতে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তটি তাই নিশ্চিত হিসেবেই পরিগণিত হয়। যুক্তিবাক্য যদি সত্য হয়, তাহলে সিদ্ধান্তটিও অবশ্যই সত্য হবে। কিন্তু কার্যকারণ সম্বন্ধের ক্ষেত্রে এরূপ দাবি করা সংগত নয়। কারণ থেকে নিঃসৃত কার্যটি সবসময়ই সম্ভাবনামূলক, নিশ্চিত নয়। কারণ, কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠ আওতাভুক্ত নয়। তা আরোহ অনুমানেরই আলোচ্য বিষয়। আরোহ অনুমানের সাহায্যেই আমরা বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের ওপর নির্ভর করে কার্যকারণের মাধ্যমে একটি সামান্য বচন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করি। আর আরোহ অনুমান যেহেতু সবসময় সম্ভাবনাময়, সেহেতু কার্যকারণের বিষয়টিও সবসময়ই সম্ভাব্য, কখনোই অনিবার্য নয়।
নিশ্চয়তার বিষয়টি যাচাইযোগ্য নয়:
কার্য ও কারণের ক্ষেত্রে অনিবার্য সংযোগ তত্ত্বের বিষয়ে এই অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে যে, কার্য এবং কারণের সম্বন্ধের কোনো নিশ্চিত নিয়ম আছে কি না তা পরিপূর্ণভাবে যাচাই করা সম্ভব নয়। কারণ, কার্যকারণ ভিত্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যে সার্বিক নিয়ম রচনা করি, তা প্রকৃতপক্ষে একটি বৈজ্ঞানিক প্রকল্প মাত্র। আবার আমরা এও জানি যে, কোনো বৈজ্ঞানিক প্রকল্পকেই পরিপূর্ণভাবে যাচাই করা যায় না। কারণ সেই প্রকল্পটির অধীনস্থ যে সমস্ত দৃষ্টান্ত আছে তাদের সংখ্যার কোনো শেষ নেই। এই অসংখ্য দৃষ্টান্তের যাচাই কখনোই সম্ভব নয়।
অনিবার্য সম্পর্কের দাবি অযৌক্তিক:
কোনো কার্য যদি কোনো কারণ থেকে যথাযথরূপে এবং অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়, তাহলেও তাদের মধ্যে যে অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ আছে- -এ দাবি করা সংগত নয়। এর কারণ হল, কারণটি সব সময়েই যে কার্যের অনিবার্য শর্ত রূপে পরিগণিত হবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণটি কখনো কখনো পর্যাপ্ত শর্ত রূপেও পরিগণিত হতে পারে। পর্যাপ্ত শর্তের ক্ষেত্রে কারণ থেকে কার্যটি যে ঘটবেই, এমন দাবি করা যায় না। অবশ্য অনিবার্য শর্তরূপী কারণ থেকে কার্যটি ঘটবেই। অন্যভাবে বলা যায় যে, ওই কারণটি না থাকলে কার্যটিও ঘটবে না। কিন্তু এই ধরনের অনিবার্য কার্যকারণের সম্বন্ধটি সব সময় লক্ষ করা যায় না। সুতরাং, কার্য ও কারণের মধ্যে অনিবার্য সম্পর্কের দাবিটি আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়।
প্রসক্তি তত্ত্বের মূল্যায়ন (Evaluation of Entailment Theory)
প্রসক্তি মতবাদের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত ত্রুটিগুলি লক্ষ করা গেলেও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে এই মতবাদকে গুরুত্বহীন বলা যায় না। কারণ, বুদ্ধিবাদী ও বিচারবাদী দার্শনিকরা বলেন—এই মতবাদকে অস্বীকার করলে যে সমস্যাগুলি দেখা যায়, সেগুলি হল—
জ্ঞানের অগ্রগতি স্তব্ধ:
কার্য ও কারণের মধ্যে যে অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ আছে, এ কথা মেনে না নিলে কোনো প্রকার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, সামান্যীকরণ, গবেষণা এবং আরোহমূলক সামান্যীকরণ আদৌ সম্ভব নয়। আর এগুলি যদি অসম্ভব হয়, তাহলে আমাদের জ্ঞান প্রক্রিয়াটিই অচল হয়ে যায়, জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের সমস্ত প্রকার অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে পড়ে। প্রত্যেকটি কার্যের একটি কারণ আছে এবং তাদের সম্পর্ক হল অনিবার্য সম্পর্ক— এরকম একটি পূর্বতসিদ্ধ অনুসিদ্ধান্তকে মেনে না নিলে আমরা জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে এক পাও এগিয়ে যেতে পারি না। এমন হলে জ্ঞানের অগ্রগতির সব দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং জ্ঞানের অগ্রগতির প্রয়োজনে এই সম্বন্ধকে স্বীকার করতেই হবে।
পূর্বতসিদ্ধ পূর্বস্বীকৃতির অভাৰ :
কোনো বিজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধভাবে পূর্বতসিদ্ধ বিষয়সমূহ (axioms)-কে মেনে না নিলে, তার আলোচনা শুরু করতে পারে না, তেমনি কার্যকারণের অনিবার্য সম্বন্ধকে মেনে না নিলে যুক্তিবিজ্ঞান এবং অপরাপর বিজ্ঞানও বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না। তাই কার্যকারণ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে প্রসক্তির তত্ত্বের গুরুত্ব কখনোই অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতপক্ষে, প্রসক্তি তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা হল অপরিসীম।
কার্যকারণ সম্পর্কে প্রসক্তি সম্বন্ধ বা অনিবার্য সম্বন্ধ মতবাদ