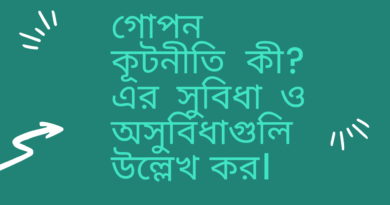পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার বিবরণ | Give an account of the system of rural self-government in West Bengal
পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার বিবরণ | Give an account of the system of rural self-government in West Bengal
উত্তর। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হােল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা। লর্ড ব্রাইসের (Bryce) মতে, “গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রয়ােজন” (Democracy needs local self-government as its fondation.)। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে জনগণ প্রশাসনিক কার্যে প্রত্যক্ষভাবে আংশগ্রহণের এবং নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মেটাবার সুযােগ পাবে। এর ফলে আত্মনির্ভরশীলতা ও নাগরিক চেতনার সম্প্রসারণ ঘটবে, যা গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য ভীষণভাবে জরুরী। এককথায়, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি গণতন্ত্রের সুতিকাগার হিসাবে কাজ করে।
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রয়ােজনীয়তায়, উদ্বুদ্ধ হয়ে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত আইন প্রণীত হয় ১৯৫৬ সালে এবং জেলা পরিষদ আইন প্রণীত হয় ১৯৬৩ সালে। এই দুই আইনের ওপর ভিত্তি করে পশ্চিমবঙ্গে চার-স্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যথাগ্রামসভা, অঞ্চল পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা পরিষদ।
এই চার স্তরের পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির নিজেদের মধ্যে ঠিকমত পারস্পরিক বােঝাপড়া গড়ে না ওঠায় এবং এগুলির ওপর অতিবেশি সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে, পশ্চিমবঙ্গে চারস্তরের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সফল হতে পারে নি। এই ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালে নতুন করে পঞ্চায়েত আইন (West Bengal Panchayat Act, 1973) প্রণীত হয়। এই নতুন আইনে পূর্ববর্তী চার-স্তরের বদলে ত্রি-স্তরের পঞ্চায়েত গঠনের কথা ঘােষিত হয় এবং আরও কিছু গুণগত পরিবর্তন ঘটানাের কথা ঘােষণা করা হয়। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে এই নতুন পঞ্চায়েত আইনটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার অব্যবহিত পরেই ১৯৭৮ সালে এই নতুন পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নতুন আইন অনুসারে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক পর্যায়ে পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা স্তরে জেলা পরিষদ।
পশ্চিমবঙ্গের স্বায়ত্তশাসন গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা
(i) গ্রাম পঞ্চায়েত : নতুন আইন অনুসারে একটি মৌজা বা তার অংশবিশেষ বা একাধিক পরস্পর সংলগ্ন মৌজাকে নিয়ে এক একটি গ্রাম গঠিত হবে এবং প্রতিটি গ্রামের জন্য গ্রামের নাম অনুসারে একটি করে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হবে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা হবে ৫ থেকে ২৫-এর মধ্যে। সদস্যগণ সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভােটাধিকারের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট গ্রামের বিধানসভার নির্বাচকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। কোন্ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা কত হবে তা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক স্থির করেন। সাধারণত প্রতি ৫০০ জন ভােটদাতা পিছু একজন প্রতিনিধি গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচিত হন।
১৯৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে (সংশােধিত) তফসিলী জাতি, উপজাতি ও মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের একতৃতীয়াংশ সদস্য মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত।
১৯৮৩ সালের সংশােধিত পঞ্চায়েত আইনে সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ পূর্বেকার চার বছরের জায়গায় পাঁচ বছর করা হয়েছে। তবে এই সময়ের মধ্যে ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হলে বা গ্রাম পঞ্চায়েতের পরপর তিনটি বৈঠকে অনুপস্থিত হলে অথবা প্রদেয় কর বা ফি না দিলে কোন সদস্যকে মহকুমা শাসক অপসারণ করতে পারেন।
গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে থেকে একজন প্রধান এবং একজন উপপ্রধান নির্বাচিত করেন। প্রধান এবং তার অনুপস্থিতিতে উপপ্রধান পঞ্চায়েতের
সভায় সভাপতিত্ব করেন। মাসে অন্তত একবার গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিবেশন আহ্বান করতে হয়।
১৯৯৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশােধনী) আইনে গ্রাম সংসদ ও গ্রামসভা গঠনের কথা বলা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় একটি গ্রাম সংসদ থাকবে। এই গ্রাম সংসদের সদস্য হবে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার ভােটদাতাগণ। গ্রাম সংসদের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি হল : (ক) নিজ এলাকার উন্নয়ন ও ন্যায় বিচারের প্রশ্নে প্রয়ােজনীয় নির্দেশ ও উপদেশ দেওয়া ; (খ) বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যাপারে উপভােগকারীদের কমিটি (Beneficiary Committee) গঠন করা ; (গ) পরিবার কল্যাণ, শিশু কল্যাণ, বয়স্ক শিক্ষা প্রভৃতি কর্মসূচিব ক্ষেত্রে গণ-উদ্যোগ সৃষ্টি করা ; (ঘ) সামাজিক সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রসার ঘটানাে, এবং (ঙ) সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যাবলী পর্যালােচনা করা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলােচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। গ্রামসভা গঠিত হয় প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সকল ভােটদাতাকে নিয়ে। গ্রাম সভা গ্রাম সংসদের আলােচনা ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপন করতে পারে। এছাড়া গ্রাম পঞ্চয়েতের বাজেট, কর্মসূচি, কাজের পরিকল্পনা, সর্বশেষ অডিট প্রভৃতি গ্রাম সভাতে পেশ করতে হয়।
গ্রাম পঞ্চায়েতের দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন কর্মসচিব (Secretary), একজন কর্ম সহায়ক (Job Assistant) থাকেন। এছাড়া পঞ্চায়েত কর্তৃক নিযুক্ত চৌকিদার, দফাদার এবং অন্যান্য কর্মচারীও থাকেন।
গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা ও কার্যাবলী :
গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে মূলত তিন ভাগে ভাগ রা যায়—(১) অবশ্য পালনীয় কার্য, (২) অন্যান্য অর্পিত কার্য এবং (৩) স্বেচ্ছাধীন কার্য।
অবশ্য পালনীয় কার্যাবলী :
১. জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, ময়লা নিষ্কাশন, জল নিষ্কাশন করা ;
২. ম্যালেরিয়া, গুটি বসন্ত, কলেরা ও অন্যান্য মহামারী নিবারণের ব্যবস্থা করা ;
৩. পানীয় জল সরবরাহ, জলাধার পরি ও তা জীবাণুমুক্ত রাখা।
৪. জলপথ রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও নির্মাণ করা ;
৫. জনপথ ও সার্বজনীন স্থানে অবৈধ দখল অপসারণ করা ;
৬. গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিকানাধীন ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি সংরক্ষণ করা ;
৭. সার্বজনীন পুষ্করিণী, সাধারণ গােচারণ ক্ষেত্র, শ্মশানঘাট এবং সার্বজনীন কবরখানা চালনা ও তত্ত্বাবধান করা ;
৮ জেলাশাসক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কোন কিন্তু সম্পর্কে তথ্য জানতে চাইলে তা সরবরাহ করা ;
৯. সমাজ ও অঞ্চলের উন্নতির জন্য স্বেচ্ছাশ্রম সংগঠিত করা ;
১০, গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা। ;
১১ পঞ্চায়েত আইন অনুসারে কর, অভিকর (lce), মাশুল (rates) ইত্যাদি আরােপ করা ও সংগ্রহ করা;
১২. দফাদার ও চৌকিদারদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা ;
১৩ •ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন ও পরিচালনা করা।
অর্পিত কার্য: রাজ্য সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর যেসব কাজের দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে সেগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।
১. বিভিন্ন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।
২.স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান নির্ণয় করা
৩. খেয়াঘাট পরিচালনা করা;
৪. জলসেচের ব্যবস্থা করা;
৫. রুগ্ন ও অনাথদের তত্ত্বাবধান করা;
৬. বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন করা ;
৭. উন্নততর গবাদি পশুর প্রজনন, চিকিৎসা ও রােগ প্রতিরােধের ব্যবস্থা করা ;
৮. পতিত জমি উদ্ধার ও সেখানে চাষের ব্যবস্থা করা ;
৯. ভূমি সংস্কার আইন বাস্তবায়নে সাহায্য করা ;
১০. গ্রামীণ গৃহ নির্মাণ কর্মসূচি গ্রহণ করা ; ইত্যাদি। ;
৫. রুগ্ন ও অনাথদের তত্ত্বাবধান করা
স্বেচ্ছাধীন কার্য : যেসব কার্য গ্রাম পঞ্চায়েত স্বেচ্ছায় সম্পাদন করে সেগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । তবে এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোন নির্দেশ থাকলে তা পালন করা বাধ্যতামূলক। স্বেচ্ছাধীন কার্যগুলি হল :
১. জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত সড়কে আলাের ব্যবস্থা করা ;
২. সর্বজনীন স্থানে বৃক্ষরােপন ও সংরক্ষণ করা ;
৩. কূপ ও পুষ্করিণী খনন করা ;
৪. সমবায়মূলক কৃষি ও বিপণন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা ;
৫. বাজার স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ, মেলা ও হাট স্থাপন, স্থানীয় কৃষিজাত ও হস্তশিল্পজাত সামগ্রীর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা ;
৬. কুটির শিল্পের উন্নয়ন সাধন করা ;
৭. সরাইখানা, ধর্মশালা, বিশ্রামাগার, গবাদি পশুর গােয়াল ইত্যাদি নির্মাণ ও তত্ত্বাবধান করা ;
৮. গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপন ও পরিচালনা করা ;
৯, চুরি-ডাকাতি নিবারণে প্রয়ােজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ইত্যাদি।
উপরােক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে আরও কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যথা-(১) গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমতি না নিয়ে কোন ব্যক্তি পঞ্চায়েতের এলাকার মধ্যে ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে পারবে না। (২) কোন ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জলাশয় বা পুষ্করিণী কোনভাবে দূষিত হলে পঞ্চায়েত তার মালিককে জল পরিশােধন করতে নির্দেশ দিতে পারে। (৩) জনস্বাস্থ্য ভঙ্গ হতে পারে এরূপ কোন কাজ কেউ করলে পায়েত তাকে বিরত করতে নােটিশ জারি করতে পারে। (৪) রাজা-সরকার যে-কোন সরকারী সম্পত্তির আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে অর্পণ করতে পারে। (৫) প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত যে-কোন দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে।
আয়ের উৎস ও গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের উল্লেখযােগ্য উৎসগুলি হল : (১) কেন্দ্রীয়
বা রাজ্য সরকার বা জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে প্রাপ্ত অনুদান, (২) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক আরােপিত কর ও ফী থেকে প্রাপ্ত অর্থ, (৩) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার থেকে সংগৃহীত ঋণ, (৪) কোন দান থেকে সংগৃহীত তার্থ, (৫) জরিমানা থেকে অর্জিত আয়, (৬) অন্যান্য উৎস থেকে অর্জিত আয় ইত্যাদি।
ন্যায় পঞ্চায়েত ঃ ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকার যদি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোন গ্রাম পঞ্চায়েতকে ন্যায় পঞ্চায়েত গঠনের অনুমতি দেয় তাহলে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন করতে পারবে। ন্যায় পঞ্চায়েত গঠনের উদ্দেশ্য হল স্বল্প খরচে দ্রুত গ্রামীন মানুষদের ন্যায় বিচার লাভের সুযােগ করে দেওয়া। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্বাচিত ৫ জন সদস্য নিয়ে ন্যায় পঞ্চায়েত গঠিত হয়। ন্যায় পঞ্চায়েতের কার্যকলাপের মেয়াদ ৫ বৎসর। ন্যায় পঞ্চায়েতের দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় এলাকাই আছে। যে সকল দেওয়ানী বিবাদের সঙ্গে ২৫০ টাকা বা তার কম টাকার প্রশ্ন জড়িত সেই সমস্ত বিবাদ ন্যায় পঞ্চায়েতের দেওয়ানী এলাকার অন্তর্ভুক্ত। গবাদি পশুর অনধিকার প্রবেশ জনিত ক্ষতি পূরণের মামলা, ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে সর্বাধিক ৫০ টাকা জরিমানা হতে পারে এমন মামলা, খেয়া আইন-সংক্রান্ত কয়েকটি মামলা ইত্যাদি ন্যায় পঞ্চায়েতের ফৌজদারী এলাকার অন্তর্ভুক্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখযােগ্য, পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত কোন ন্যায় পঞ্চায়েত নেই।
পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় পঞ্চায়েত সমিতি
(ii) পঞ্চায়েত সমিতি : পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে পঞ্চায়েত সমিতি প্রতিটি ব্লকের জন্য একটি করে পঞ্চায়েত সমিতি থাকবে। ব্লকের অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানগণ, ব্লক এলাকা বা তার কোন অংশ থেকে নির্বাচিত বিধানসভা ও লােকসবার সদস্যগণ, ব্লক এলাকার অন্তর্গত প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত অনধিক তিনজন সদস্যকে নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতি গঠিত হয়। নতুন পঞ্চায়েত আইন অনুসারে পঞ্চায়েত সমিতির মােট আসনের এক-তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত।
পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্যগণের কার্যকালের মেয়াদ ৫ বৎসর। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যগণের মধ্য থেকে একজন সভাপতি ও একজন সহসভাপতি নির্বাচিত হন। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (B.D.O.) পদাধিকার বলে পঞ্চায়েত সমিতির কার্যনির্বাহী আধিকারিক (Executive Officer)। প্রতি তিনমাস অন্তর পঞ্চায়েত সমিতির সভা আহ্বান করতে হয়।
সুষ্ঠুভাবে এবং দ্রুততার সঙ্গে কার্য পরিচালনার জন্য পঞ্চায়েত সমিতির কয়েকটি স্থায়ী সমিতি রয়েছে, যথা—(১) অর্থ ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি, (২) জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি, (৩) পূর্ত ও পরিবহন স্থায়ী সমিতি, (৪) কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি, (৫) শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি, (৬) বন ও ভূমিসংস্কার স্থায়ী সমিতি, (৭) খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতি, (৮) মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ স্থায়ী সমিতি ইত্যাদি।
পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী :
পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান প্রধান কাজগুলি হল ঃ (১) কৃষি, কুটির শিল্প, সাবা, পশুপালন, গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থা, জল সরবরাহ, জলসেচ, হাসপাতাল, জনস্বাস্থ্য, যোগাযােগ, প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষা, ছাত্রকল্যাণ, সমাজকল্যাণ প্রভৃতির প্রসার, উন্নয়ন ও সেই উদ্দেশ্যে প্রকল্প গ্রহণ এবং আর্থিক সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করা (২) রাজ্য সরকার কর্তৃক আরােপিত যে কোন প্রকল্প বা কার্যক্রম বাস্তবায়িত করা ; (৩) পঞ্চায়েতের অধীনস্থ যে কোন বিদ্যালয় অথবা জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান করা ; (৪) আর্তদের ত্রাণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা ; (৫) ব্লকের অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা ; (৬) পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির বাজেট পরীক্ষা ও অনুমােদন করা। এছাড়াও রাজ্য সরকার ও জেলাপরিষদ কর্তৃক আরােপিত দায়িত্ব পঞ্চায়েত সমিতিগুলি সম্পাদন করে।
পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার বিবরণ
আয়ের উৎস : পঞ্চায়েত সমিতির আয়ের প্রধান উৎস হল সরকারী অনুদান, অর্থ সাহায্য ও ঋণ। জেলা পরিষদও সমিতিকে অর্থ সাহায্য করতে পারে। এছাড়া হাটবাজারের ওপর ধার্য লাইসেন্স ফী, যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফী, ফেরিঘাট ও যানবাহনের ওপর ধার্য শুল্ক, টোল ট্যাক্স, জল সরবরাহ ও রাস্তাঘাট আলােকিত করার জন্য ধার্য অভিকর (rate) ইত্যাদি থেকেও সমিতির আয় হয়ে থাকে।
পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় জেলা পরিষদ
(iii) জেলা পরিষদ : পঞ্চায়েত ব্যবস্থার তৃতীয় এবং সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে জেলা পরিষদ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সতেরােটি জেলার মধ্যে কলকাতা ও দার্জিলিং ব্যতীত ১৫টি জেলায় জেলা পরিষদ রয়েছে। জেলা পরিষদ গঠিত হয় নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে ।
(১) জেলার অন্তর্গত প্রতিটি ব্লক থেকে বিধানসভার নির্বাচকগণ কর্তৃক নির্বাচিত ২ জন সদস্য ; (২) জেলার অন্তর্গত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিগণ ; (৩) মন্ত্রিগণ ছাড়া জেলা থেকে নির্বাি লােকসভা ও বিধানসভার সদস্যগণ এবং (৪) জেলাতে বসবাসকারী মন্ত্রী ছাড়া রাজ্যসভার সদস্যগণ। জেলা পরিষদের মােট আসন সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত থাকে।
পদাধিকারবলে-নিযুক্ত সদস্যগণ ছাড়া জেলা পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর। জেলা পরিষদের প্রথম অধিবেশনে সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজন সভাধিপতি এবং একজন সহকারী সভাধিপতি নির্বাচন করেন। সভাধিপতি হলেন জেলা পরিষদের প্রশাসনিক প্রধান। তার তত্ত্বাবধানেই জেলা পরিষদের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালিত হয়।
জেলা পরিষদের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক একজন কার্যনির্বাহী আধিকারিক (Executive Officer) একজন অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিক (Additional Executive Officer) নিয়ােগ করা হয়।
জেলা পরিষদের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পঞ্চায়েত সমিতির ন্যায় জেলা পরিষদের অর্থ, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য, পূর্ত কার্য, কৃষি সেচ ও সমবায়, শিক্ষা, ক্ষুদ্র শিল্প এবং ত্রাণ ও জনকল্যাণ বিষয়ে স্থায়ী কমিটি আছে।
জেলা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী
পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার বিবরণ
জেলা পরিষদের প্রধান প্রধান কাজগুলি হল ঃ (১) কৃষি, পশুপালন, কুটির শিল্প, সমবায় আন্দোলন, গ্রামীণ ঋণ, জল সরবরাহ, সেচ, জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা, ছাত্রকল্যাণসহ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বয়স্ক শিক্ষা, সামাজিক সমৃদ্ধি এবং অন্যান্য সার্বিক জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রকল্প গ্রহণ ও আর্থিক সাহায্য প্রদান ; (২) রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পকে সফল করা এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক আরােপিত দায়িত্ব গ্রহণ;
(৩) জেলার মধ্যে অবস্থিত বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার ও জনহিতকর সংগঠনকে অনুদান প্রদান ; (৪) প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটানাে ; (৫) গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিকে আর্থিক অনুদান প্রদান ; (৬) জেলার মধ্যে অবস্থিত পৌরসংস্থাগুলিকে জল সরবরাহ বা মহামারী প্রতিরােধে অর্থ সাহায্য প্রদান ; (৭) জেলার মধ্যে অবস্থিত পঞ্চায়েত সমিতিগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং জেলাস্তরে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ; (৮) জেলার মধ্যে অবস্থিত পঞ্চায়েত সমিতিগুলির আয় ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা ও অনুমােদন করা, ইত্যাদি।
আয়ের উৎস ঃ জেলা পরিষদের আয়ের প্রধান প্রধান উৎসগুলি হলঃ (ক) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার প্রদত্ত অনুদান, (খ) রাজ্য সরকার প্রদত্ত ভূমি রাজস্বের অংশ, (গ) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার প্রদত্ত ঋণ, (ঘ) পথ কর, পূর্ত কর এবং লাইসেন্স ফী থেকে সংগৃহীত অর্থ, (ঙ) দান বা সাহায্য থেকে প্রাপ্ত অর্থ, (চ) জেলা পরিষদ পরিচালিত কলকারখানা, প্রতিষ্ঠান, বিশ্রামাগার থেকে আয়, (ছ) জরিমানা থেকে সংগৃহীত অর্থ, ইত্যাদি।
মূল্যায়ন ও গণতন্ত্রকে তৃণমূলে পৌঁছে দেওয়া, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটানাে, প্রশাসনিক কার্যে জনগণের অংশগ্রহণের সুযােগ সৃষ্টি করা, গ্রামীণ মানুষের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা ও নাগরিক চেতনার সম্প্রসারণ ঘটানাে ইত্যাদি যে মহান আদর্শ ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করা হয়, সমালােচকদের মতে, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি সেইসব লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে নি এবং সাধারণ মানুষের প্রত্যাশাগুলি পূরণ হয় নি।
সমালােচকদের প্রধান অভিযোেগ এই যে, পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর মাত্রাতিরিক্ত সরকারী নিয়ন্ত্রণ পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিকে পঙ্গু করে দিয়েছে এবং স্বায়ত্ত শাসনের লক্ষ্যে পৌঁছানাের পথে প্রধান অন্তরায় হিসাবে কাজ করেছে। পঞ্চায়েতের ওপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রধানত ২ ধরনের—(ক) আর্থিক এবং (খ) প্রশাসনিক। পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক অনুদান, ঋণদান, পঞ্চায়েতের হিসাব-নিকাশ পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক হিসাব পরীক্ষক নিয়ােগ ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হয়। আর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে কর্মচারী নিয়ােগ, পঞ্চায়েত সংস্থার যে কোন প্রস্তাব বা কর্মসূচিকে অনুমােদন অথবা বাতিল, পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর বিশেষ বিশেষ কাজের দায়িত্ব অর্পণ এবং তা পালনে বাধ্য করা, পঞ্চায়েতের যাবতীয় কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করার জন্য আধিকারিক নিয়ােগ—ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার তার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।
দ্বিতীয়ত, যে সার্বিক উদ্যোগ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, সেই পরিমাণ উদ্যোগ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ গ্রামের মানুষের মধ্যে দেখা যায় না বলে সমালােচকদের অভিযােগ।
পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার বিবরণ
তৃতীয়ত, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও রূপায়ণ, বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি ব্যাপারে যে বিশেষ দক্ষতা ও জ্ঞানের প্রয়ােজন পঞ্চায়েত সদস্যদের মধ্যে তা থাকে না। এছাড়া দুর্নীতি, সরকারী অর্থের অপচয়, পঞ্চায়েত সদস্যদের অতি বেশি সরকারের
মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার মানসিকতা, নেতৃত্বের সঙ্কট, পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর গ্রামের বিত্তবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাব–ইত্যাদি নানা অভিযােগ শােনা যায়।
উপরােক্ত অভিযােগগুলির মধ্যে যে সত্যতা নেই তা নয়, তবে একথা মনে করলেও ভুল হবে যে, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গ্রামের রাস্তাঘাট নির্মাণ, ভূমি সংস্কার ও উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন, নানাবিধ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনও করে চলেছে।
পশ্চিমবঙ্গের স্বায়ত্তশাসন
অপারেশন বর্গা’ কার্যকর করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি অন্য যে কোন রাজ্যের থেকে বেশি কৃতিত্বের দাবি করতে পারে।
১৯৭৮ সালের বিধ্বংসী বন্যা এবং ১৯৮২ সালের অভূতপূর্ব খরা পরিস্থিতিকে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা যেভাবে মােকাবিলা করেছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে।
পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার বিবরণ
সবশেষে, আজ গ্রাম বাংলার খেটে খাওয়া মানুষদের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদাবােধ গড়ে উঠেছে তা অনেকখানি এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থারই কল্যাণে। ভারতের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুরেন্দ্রকুমার দে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার
সাফল্যে মন্তব্য করেন যে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ মানুষের জন্য পঞ্চায়েত যা কাজ করেছে তা ইতিহাসে বিরল। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, নােবেল জয়ী অমর্ত্য সেন, নেইল ওয়েবস্টার প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন।
পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার বিবরণ